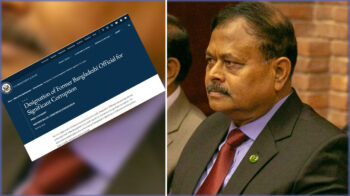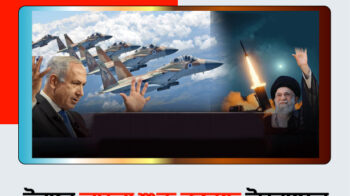ডেস্ক নিউজ:
মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ একটি ইস্যুকে সামনে তুলে এনেছে; শরণার্থী সঙ্কট হিসাবে আবির্ভূত হওয়া এই সমস্যা শিগগিরই যে সমাধান হবে তারও কোনো ইঙ্গিত মিলছে না। এই ইঙ্গিত না মেলার পেছনে একটি বিষয় কাজ করছে। সেটি হলো দেশটির নির্বাচিত সরকার ও প্রভাবশালী সেনাবাহিনীর মধ্যকার সম্পর্ক।
সঙ্কটের শুরুর দিকেই আন্তর্জাতিক সমালোচকরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনা-অভিযানের জন্য রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা অং সান সু চিকেই দোষারোপ করেছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসে গত ৭ সেপ্টেম্বর লেখা এক নিবন্ধে জ্যাকব জুদাহ সু চির ১৯৯১ সালে পাওয়া নোবেল পুরস্কার প্রত্যাহার করে নেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। অং সান সু চি ও মিয়ানমারের জেনারেলদের উল্লেখ করে জ্যাকব বলেন, রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা হিসাবে সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখেন সু চি।
এমনকি ৯ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসে অপর এক নিবন্ধ লেখেন নিকোলাস ক্রিস্টফ। তার লেখা শুরু হয়েছে, ‘নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী প্রিয় অ সান সু চি জাতিগত নিধন অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যে অভিযানে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, নারীদের ধর্ষণ এবং শিশুদের কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এর এক সপ্তাহ পর জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরাস শরণার্থী সঙ্কট সমাধানে সু চির জন্য শেষ সুযোগ বলে সতর্ক করে দেন।
আইন অনুযায়ী যদিও সামরিক বাহিনীর ওপর সু চির কোনো ক্ষমতা নেই; যার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে আছেন সেনাপ্রধান মিন অং হ্লেইং। রোহিঙ্গাদের প্রতি নিষ্ঠুর অভিযানের জন্য সু চির সমালোচনা শুরু হলেও চলতি বছরের আগস্টের আগে এপ্রিলে সেনাপ্রধান মিন অং হ্লেইং অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি সফরে যান। জুনে রাশিয়া, জুলাইয়ে ভারত এবং আগস্টে জাপান সফর করেন। প্রত্যেকটা দেশেই তিনি লাল-গালিচা সংবর্ধনা পেয়েছেন। তবে এই সফরে রোহিঙ্গা সঙ্কট থেকে শুরু করে কাচিন, পলং ও সংখ্যালঘু শান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা তিনি একবারের জন্য উচ্চারণ করেননি।
সমালোচকরা যুক্তি দিয়ে বলছেন, মিয়ানমারের বেসামরিক এবং সামরিক সম্পর্কের ধরন এবং দেশটির নির্বাচিত সরকারের আসলে কতটুকু ক্ষমতা রাখে তা নিয়ে বাইরের দুনিয়ায় ভুল বোঝাবুঝি আছে।
২০১০ সালের নভেম্বরে যখন দেশটিতে সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের অধীনে আধা-বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়। সেই সময় সরকার গঠনকে অনেকেই দেশটিতে নতুন এবং অধিক উদার রাজনৈতিক যুগের সূচনা বলে মন্তব্য করেন।
পরবর্তীতে বন্দিদের মুক্তি, গণমাধ্যমের নজিরবিহীন স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার অবাধ সুযোগ দেয়ার মতো বিষয়গুলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তা রবার্ট কুপার ‘মিয়ানমারের বার্লিন প্রাচীর মুহূর্ত’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
মিয়ানমারের সাবেক সেনাপ্রধান থেইন সেইনকে সেই সময় ‘মিয়ানমারের মিখাইল গর্বাচেভ’ হিসাবে উল্লেখ করে অনেকেই প্রশংসা করেন। তবে গুঞ্জন আছে, পুরনো সেনা শাসকদের সঙ্গে কট্টরপন্থী ও সংস্কারকামীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ছিল।
স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হলেও মিয়ানমারে তেমন কোনো পরিবর্তন দৃশ্যমান নয়। তবে একধরনের নতুন হাইব্রিড রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান ঘটেছে; যার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আছে সেনাবাহিনী। দেশটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে। অন্যদিকে নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিদের হাতে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কিছু ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতি।
২০০৮ সালের মে মাসে প্রতারণামূলক গণভোট অনুষ্ঠানের পর ২০১০ সালের নির্বাচনের আগে সামরিক সরকারের অধীনে নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। সংবিধানের প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়, ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকায় অংশ নেয়ার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা যাবে। এই অধ্যায়ে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসনসহ সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।
সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে সংসদের ২৫ শতাংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়। একই সঙ্গে এই সংবিধানে সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলেও সেনাবাহিনীর অনুমোদন নেয়ার বিধান করা হয়। সেনাবাহিনীর হাতে রয়েছে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। দেশটির রাজ্য থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের এমনকি জেলা থেকে উপ-শহরের মতো সব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ (জিএডি)।
গত ৫৪ বছরের মধ্যে প্রথম বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে ২০১৬ সালের এপ্রিলে। সু চির নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) আগের বছরের এপ্রিলে দেশটির সাধারণ নির্বাচনে ভূমিধস জয় লাভ করে। তবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীর নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের দ্বরাই চলছে; যাদের অনেকেই আগের সামরিক জান্তা সরকারের আমলে চাকরি করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে বেসামরিক সরকারের ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে একেবারেই নগণ্য।
কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে সু চির হাত পুরোপুরি বাঁধা। সমালোচকরা যুক্তি দিয়ে বলছেন, সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানানো ছাড়াই রাখাইন সফর করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারতেন। রাখাইন সফরের মাধ্যমে তিনি মিয়ানমারের বেসামরিক সরকারের সীমিত পরিসরের রাজনীতির প্রসার ঘটাতে পারতেন।
তিনি হয়তো মৌলবাদী রাখাইন জাতীয়তাবাদীদের পছন্দ করেন না। কিন্তু এ ধরনের সফরের মাধ্যমে তিনি জনগণকে দেখাতে পারতেন যে, মিয়ানমারের সরকার ব্যবস্থায় একটি বেসামরিক অঙ্গ আছে। তিনি রাখাইনের সহিংসতায় আহত হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানদের দেখতে হাসপাতালে যেতে পারতেন। বৃহৎ অর্থে তিনি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারতেন।
কিন্তু গত বছর থেকে তার নেতৃত্বের ধরন দলের অনেক সমর্থককেও হতাশ করেছে। রাজধানী নেইপিদোতে তিনি সন্ন্যাস জীবন-যাপন করছেন। ২০১৫ সালে দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের জন্য যে জনগণ তাকে ভোট দিয়েছিলেন; তিনি তাদের থেকে দূরে সরিয়ে আছেন। রোহিঙ্গা সঙ্কটে সেনাবাহিনীর অভিযানে নীরব থাকায় সু চির যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সু চির ফেসবুক পেইজে এবং অফিসের ওয়েবসাইটে বিতর্কিত বিবৃতিগুলোর অধিকাংশই তার লেখা নয়; তার উপদেষ্টা জ্য হতেই এসব বিবৃতি লেখেন। সু চির এই উপদেষ্টা দেশটির সাবেক জান্তা সরকারের একজন সেনা কর্মকর্তা; যিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনেরও উপদেষ্টা ছিলেন।
সু চিকে ছাড়া এনএলডি আগামী ২০২০ সালের নির্বাচনে তেমন কোনো সুবিধা করতে পারবে না; যেমনটা করেছে ২০১৫ সালের নির্বাচনে। রাজনীতিতে মিয়ানমারের এই নেত্রী না থাকলে তার জায়গা দখল করার মতো কিংবা নেতৃত্ব দেয়ার মতো তরুণ প্রজন্মের কোনো রাজনৈতিক কর্মী সু চি কিংবা এনএলডি এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি।
সু চির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে আবারো এনএলডিকে শোষণ কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা রয়েছে সেনাবাহিনীর।